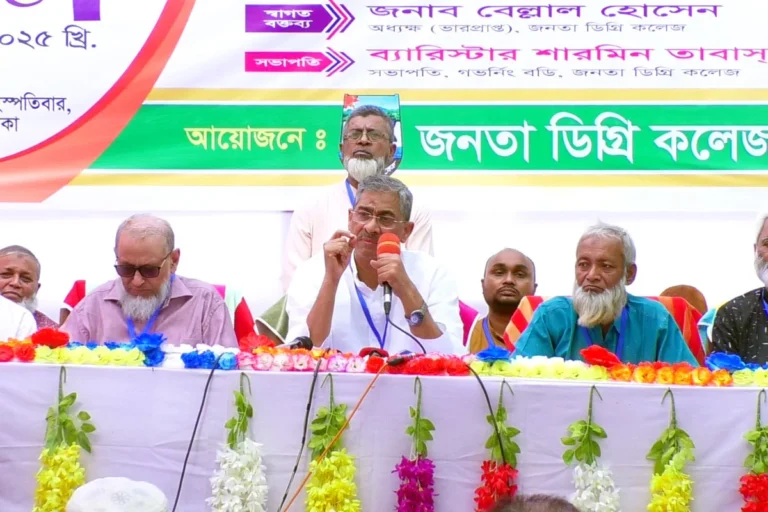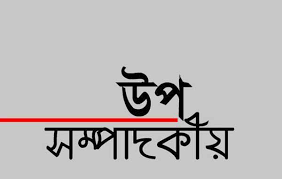
রুদ্র মোহাম্মদ ইদ্রিস॥
বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব বা স্থানীয় ক্ষমতার লড়াই কোনো নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় এই দ্বন্দ্ব যে ভয়াবহ ও রক্তাক্ত রূপ নিয়েছে, তা গভীর উদ্বেগের বিষয়। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ব্যক্তিগত ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, ও স্থানীয় প্রভাব বিস্তারের লড়াই-সবকিছু মিলিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এখন যেন অঘোষিতভাবে “গোষ্ঠীগত সংঘর্ষের জনপদ” হয়ে উঠছে। প্রশ্ন জাগে, আমরা আসলে কোনদিকে যাচ্ছি?
গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের মূল কারণ কী?
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইতিহাস সমৃদ্ধ, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে জেলাটি একসময় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে স্থানীয় রাজনীতিতে ব্যক্তিনির্ভর ও গোষ্ঠীনির্ভর নেতৃত্বের উত্থান ঘটে। রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরে মতাদর্শিক ঐক্যের চেয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলে দলে বিভক্তি বেড়ে যায়। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে একাধিক প্রভাবশালী পরিবার বা গোষ্ঠী নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে ওঠে। স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা অনেক সময় রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠে সংঘর্ষের বলি।
দ্বন্দ্বের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব: গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ শুধু প্রাণহানি বা সম্পদ নষ্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সমাজের ভিত নষ্ট করে দেয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অনেক গ্রামে আজ মানুষ একে অপরের প্রতি অবিশ্বাসী। রাজনৈতিক কর্মীরা প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক এড়িয়ে চলছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অস্থিরতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রভাব, এমনকি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পর্যন্ত বিভাজনের প্রভাব পড়ছে। যুবসমাজের একটি অংশ এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে-যারা দেশের ভবিষ্যৎ হওয়ার কথা, তারা হয়ে উঠছে সংঘর্ষের অস্ত্রবাহক।
রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবক্ষয়ধ:
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দেখা যায়, দলীয় রাজনীতির নাম করে অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থই মুখ্য হয়ে ওঠে। দলীয় সিদ্ধান্ত বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ উপেক্ষা করে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা নিজেদের প্রভাব খাটাতে গিয়ে গোষ্ঠীভিত্তিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এভাবে রাজনৈতিক আদর্শ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ রাজনীতিকে দেখতে শুরু করেছে ভয় ও অরাজকতার প্রতীক হিসেবে।
সমাধানের পথ কোথায়?
এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো রাজনৈতিক সচেতনতা ও নেতৃত্বের জবাবদিহিতা।
১. রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব – স্থানীয় নেতৃত্ব নির্বাচনে ব্যক্তিনির্ভরতা নয়, নীতিনিষ্ঠ ও জনমুখী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
২. প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা – আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করতে দিতে হবে। দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
৩. সামাজিক ঐক্যের উদ্যোগ – স্থানীয় আলেম, শিক্ষক, সমাজকর্মী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে নিয়ে ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে হবে।
৪. যুবসমাজের সম্পৃক্ততা – তরুণদের রাজনৈতিক সহিংসতা থেকে দূরে রেখে শিক্ষা, ক্রীড়া ও উদ্যোক্তা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া এক সময় ছিল জ্ঞান, সংস্কৃতি ও আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। আজ যদি সেই জনপদ গোষ্ঠীগত হানাহানিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে সেটি শুধু জেলার নয়, গোটা জাতির পরাজয়। আমাদের এখনই আত্মসমালোচনায় ফিরতে হবে।
গোষ্ঠীর নয়-আমরা যেন মানুষ, নাগরিক ও বাঙালি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি-এই হোক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ও আমাদের সবার প্রত্যাশা।